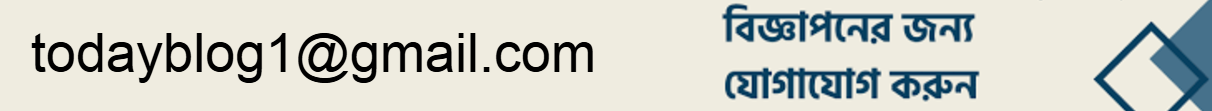তরুণ ছাত্রনেতা আবিদুল ইসলামের চোখে-মুখে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন। প্রতিহিংসাহীন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষায় বিভোর থাকতেন তিনি। এ কারণে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাজনৈতিক অঙ্গনে পা রাখেন এই ছাত্রনেতা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাস জীবনের শুরু থেকেই প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে নিজেকে হাজির রেখে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন এই তরুণ। এরই মধ্যে চব্বিশের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত যা পরবর্তীকালে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই আন্দোলনে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন তিনি। ভীষণ দুঃসময়ে সাধারণ মানুষকে এক রাখতে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘প্লিজ কেউ কাউকে ছেড়ে যাইয়েন না।’ যা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক আবেগতাড়িত বাণী।
সম্প্রতি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিজের অভিজ্ঞতা ও অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। বলেন আন্দোলনের নানা দিকের কথা।
বাসস: ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে কীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন? শুরুর দিকে আন্দোলন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ছিল?
আবিদুল ইসলাম খান: ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে আমি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলাম। স্লোগান দেওয়া, টিয়ার গ্যাস খাওয়া—সবকিছু মিলিয়ে সেই অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত। সেই আন্দোলন সরকার পর্যায়ে আলোচনার একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, যেখানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে কোটা বাতিলের যে পরিপত্র জারি হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে তা স্থগিত করে আবারও কোটা ফিরিয়ে আনা হয়। এ পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছিল ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতার আলোকে এই আন্দোলনকে আবারও জোরদার করতে হবে।
চব্বিশে যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তখন ছাত্রদলের সাথে যুক্ত থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই আমাকে চিনতেন। এ কারণে আমার সরাসরি আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না, কারণ এতে আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমি আমার জুনিয়রদের, যেমন মায়েদ, সাজ্জাদ, সাকিব বিশ্বাস—এদেরকে প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনের খোঁজ খবর রাখতে বলি। ৫ জুন তারা বিক্ষোভ মিছিলে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে।
একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা যতটা সহজ ছিল, ছাত্রদল কর্মী হিসেবে আমাদের জন্য তা ছিল ততটাই চ্যালেঞ্জিং। কারণ, ছাত্রদলকে নিয়ে বিতর্ক তৈরির একটি সুযোগ সবসময়ই খুঁজতো তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকার। একদিকে সংবাদমাধ্যমগুলো ছাত্রদলের অনুপস্থিতি নিয়ে খবর প্রকাশ করে, আবার যখন আমরা আন্দোলনে আসতে চাই, তখন বাধা দেওয়া হয় এই বলে যে ছাত্রদল আসলে আন্দোলন ভিন্ন খাতে চলে যাবে। এইরকম কঠিন পরিস্থিতি ছিল আমাদের জন্য।
এ অবস্থায় ৬ জুন আমি শহীদুল্লাহ হল ছাত্রদলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন নূরের সাথে কথা বলি। আমাদের আলোচনায় উঠে আসে যে ছাত্রদল করায় আমাদের জুনিয়ররা সরাসরি আন্দোলনে যেতে পারবে না। কারণ কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা ছাত্রদলকে দূরে রাখতে চাইবে। কিন্তু আমাদের জুনিয়রদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রয়োজন ছিল তাদের রাজনৈতিক পরিপক্কতা বাড়ানোর জন্য। পরে আমাদের আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বর্তমান দপ্তর সম্পাদক ওয়াসি তামিকে যুক্ত করি।
আমরা আলোচনা করি যে ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের পর থেকে ক্যাম্পাসে আমাদের রাজনৈতিক পদচারণা সীমিত হয়ে পড়ে। এছাড়া ২০২২ সালে ছাত্রলীগের একটি হামলার পর এটি আরও বন্ধ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে জুনিয়রদের রাজনৈতিক চর্চা এবং পরিপক্কতা অর্জনের জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরি।
আমাদের লক্ষ্য ছিল জুনিয়রদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে মিশিয়ে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো।
আমরা সিদ্ধান্ত নিই, ২০১৮-১৯ সেশন থেকে নিচের সেশনগুলো থেকে ছাত্রদল কর্মীদের এই আন্দোলনে যুক্ত করবো। আমরা যারা সিনিয়র ছিলাম তারা পেছন থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বৈরাচারী সরকারের ভুল করার সুযোগ নেওয়া। আমরা জানতাম, ফ্যাসিবাদী সরকার ভুল করবেই। সেই ভুলের সুযোগ নিতে হলে রাজনৈতিক কর্মীদের এই আন্দোলনে যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল, যেন সরকার ভুল করলে তার সুযোগ নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে ভুল করতে প্ররোচিত করা যায়।
এ আলোচনার পর আমি মায়েদ এবং সাজ্জাদকে ফোন করি। সাজ্জাদের স্মার্টফোন না থাকায় মায়েদকে বললাম একটি গ্রুপ খুলতে এবং ২০১৮-১৯ সেশন থেকে নিচের সেশনের ছাত্রদলের আগ্রহী কর্মীদের যুক্ত করতে। মায়েদ তাৎক্ষণিকভাবে একটি গ্রুপ খোলে। এরপর ভিডিও কলের মাধ্যমে আমরা এতক্ষণ যে প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম—জুনিয়রদের পরিপক্কতা, পাবলিক ফিগার হিসেবে পরিচিতি এবং সরকারের ভুল করার সুযোগ নেওয়া—সেগুলো তাদের সামনে তুলে ধরি। এর ফলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়।
জুনিয়রদের সাথে আলোচনার পর আমি আমার সাংগঠনিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের তৎকালীন সেক্রেটারি নাহিদুজ্জামান শিপনকে ফোন করে সবকিছু অবহিত করি। তিনি আমাদের পরিকল্পনায় সম্মতি দেন। ৬ই জুন থেকে আমাদের ‘কোটা আন্দোলন পর্যালোচনা গ্রুপ’ এ আলোচনা শুরু হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের ভুল করার সুযোগ নিয়ে তার পতন ঘটানো।
গত বছরের ৯ই জুন রাজু ভাস্কর্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল ছিল। যেহেতু তখন ঈদের কারণে অনেক শিক্ষার্থী বাড়িতে চলে গিয়েছিল, আমি কয়েকজন জুনিয়র ও অন্যান্যদের সাথে সমন্বয় করে ওইদিন ৪০-৫০ জনের একটি দল প্রেরণ করি। এভাবে ৯ জুন থেকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনে যুক্ত হই।
বাসস: আমরা দেখেছি, পহেলা জুলাই থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে নিয়মিত কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচিগুলোতে কীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন অথবা এই সময়টাতে কীভাবে কাজ করেছিলেন?
আবিদুল ইসলাম খান: আমাদের মূল সিদ্ধান্ত ছিল 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদেরকে তাদের মত করে কাজ করতে দেওয়া। আর আমরা ভেতরে ভেতরে নিজেদের কাজ চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ফলে তাদের কোনো কর্মসূচিতে আমরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করিনি, কারণ তারা তাদের মতো কাজ করছিল। আমরা বিশ্বাস করতাম, একটি গণঅভ্যুত্থান কখনোই একক পরিকল্পনা বা নেতৃত্বের মাধ্যমে হয় না।
আন্দোলনের শুরুর দিকে যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি গঠন করা হয় তখন আমাদের দুজন ওই কমিটিতে সহ-সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন। তারা হলেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিজভী আলম এবং স্যার এ এফ রহমান হল ছাত্রদলের সহ-প্রচার সম্পাদক মেহেদী হাসান মুন্না।
এদের মাধ্যমে আমরা ওই কমিটির সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম এবং হালনাগাদ তথ্য পেয়েছিলাম তখন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তাদের অবরোধ কর্মসূচি বা অন্যান্য কর্মসূচি পালন করেছে, আমরা সেগুলোতে কোনো হস্তক্ষেপ করিনি, বরং পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছি এবং অংশগ্রহণ করেছি। কারণ তাদের কার্যক্রম সফল হলে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এ জন্য।
আন্দোলন যখন ১লা জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগ কেন্দ্রিক তখন আমরা প্রতিদিন আমাদের ছাত্রদলের কর্মীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছি। আমি নিজে ২ জুলাই শাহবাগে ছিলাম। আমাদের জুনিয়ররা ভেতরে স্লোগান দিতো, আর আমরা তাদের জন্য পানি সরবরাহ করতাম এবং পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম।
আমাদের যে অনলাইন গ্রুপ ছিল সেটাতে আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভিডিও কলে আলোচনা করতাম। জুনিয়র যারা ছিল তাদের বলে দিতাম কীভাবে তারা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। যেমন- স্লোগান কীভাবে দিতে হবে, সাংবাদিকদের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে, এমনকি কী বলতে হবে তার স্ক্রিপ্টও আমি নিজে লিখে দিতাম। কারণ, আমাদের জুনিয়ররা তখন অতটা পরিপক্ব ছিল না এবং সামান্য ভুল হলে তখন আন্দোলনের অনেক বড় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এসব ভেবে আমি কাজটা করতাম।
৩, ৪ এবং ৫ই জুলাইয়ের পর যখন বিভিন্ন হল থেকে এবং বিভাগ ভিত্তিক মিছিল আসা শুরু হলো, তখন কিছু ছাত্রলীগ কর্মীও মিছিলে আসতো। এই ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলের ছেলেদের টার্গেট করে বুলিং করত। একবার বিজয় ৭১ হলের দপ্তর সম্পাদক সাকিব বিশ্বাসের সাথে অ্যাকাউন্টিং বিভাগের এক ছাত্রলীগ কর্মীর প্রায় হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছিল। এমন ঘটনা ঘটলে এর দায় সরাসরি ছাত্রদলের ওপর আসতো, তাই এগুলো মোকাবিলা করা আমাদের জন্য জরুরি ছিল। আমরা খুবই সচেতনতার সাথে এসব বিষয় সমাধান করেছিলাম।
আন্দোলনের শুরুর দিকে ছাত্রদলের যারা কোনো পদ পদবি ছিল না তাদেরকে স্পেস দেওয়া হচ্ছিল না। পরে আমি আখতার হোসেন ও বর্তমান উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সাথে কথা বলি। পরে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার কথা জানান তারা এবং সবাইকে স্পেস দেওয়ার কথা বলেন।
পরে ৪ জুলাই রাতে আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে ফোন আসে যে পরদিন সকালে যেন আমরা পার্টি অফিসে আসি। আমরা আট-দশজনের একটি দল কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসে যাই। সেখানে এই আন্দোলন কীভাবে হচ্ছে, কারা পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং আমাদের অংশগ্রহণ কতটুকু, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা যেভাবে এগোচ্ছি, সেভাবেই এগোতে থাকব। কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন, ‘আমরা যে ভাত খাই, সেটাও হাসিনা পতনের জন্য। তোমরা দুশ্চিন্তা করো না, এগিয়ে যাও। আমরা পাশে আছি।’
৬ই জুলাই থেকে প্রতিদিনের মতো আন্দোলন চলতে থাকে। সাক্ষাৎকার, গান, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবেও আমাদের ছেলেমেয়েরা আন্দোলনকে সচল রাখে। ৬ই জুলাই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে কোটা আন্দোলনকে সমর্থন জানান এবং শিক্ষার্থীদের দাবিকে সমর্থন করেন। ১১ই জুলাই ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। এরপর ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ই জুলাইও আমরা প্রতিদিনের মতো আমাদের কাজ করে গেছি।
বাসস: ১৪ জুলাই রাতের ঘটনাবলি বলুন।
আবিদুল ইসলাম খান: কোটা সংস্কার আন্দোলনকে আমরা প্রতিদিন জ্বালানি যুগিয়েছি, বড় করেছি এবং অন্যান্য সকল ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে এগিয়ে গেছি।
১৪ই জুলাই সকালে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতি বরাবর একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। ওইদিন এক সংবাদ সম্মেলনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কোটা পাবে না তো রাজাকারের নাতিরা কোটা পাবে?’ এই মন্তব্যের পরপরই আমরা এটিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাই। আমরা আমাদের অনলাইন গ্রুপে আলোচনা করতে থাকি।
পরে রাতে যখন হল থেকে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিতে দিতে বের হওয়া শুরু করে তখন আমি ছাত্রদলের সকল হল ইউনিটের কর্মীদের, এমনকি যারা প্রকাশ্যে আমাদের সাথে যুক্ত নয়, তাদেরও নির্দেশ দিই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য। রাতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর জসিম উদ্দিন হল, বিজয় ৭১ হল, মুহসীন হল, সূর্যসেন হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে থালা-বাসন বাজিয়ে ‘তুমি কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার’ স্লোগান শুরু হয়। ওই সময় আসলে কোনো নির্দিষ্ট নেতৃত্ব ছিল না; প্রতিটি শিক্ষার্থীই নেতা হয়ে নিজের দায়িত্বে এই রাজাকার স্লোগানটি ব্যঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহার করে।
গ্রুপে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা গ্রুপে আলোচনা করি যে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাসিনাকে ‘স্বৈরাচার’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।
আমি তাৎক্ষণিক মায়েদকে ফোন করে দ্রুত ১০ জনকে নিয়ে ‘স্বৈরাচার’ শব্দটি দিয়ে স্লোগান তৈরি করতে বলি।
একই নির্দেশ দিই মেহেদী হাসান মুন্না এবং সিফাত ইবনে আমিনকে। আমাদের অভ্যন্তরে যখন ‘স্বৈরাচার’ স্লোগান তোলার আলোচনা চলছিল, তখন ছাত্রদলের সহ-সমন্বয়ক ও জিয়াউর রহমান হল ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিজভী আলম একটি স্লোগান লিখে দেন: ‘তুমি কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার-স্বৈরাচার’।
১৪ই জুলাই রাত ১১টা ৩৪ মিনিটে সর্বপ্রথম রিজভীর এই স্লোগানটি আসে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিফাতকে ফোন করে বলি, ‘জীবন যাক বা থাক, আজ হয় মরবো নয় বাঁচব, তুই এই স্লোগানটা তুলবি।’ সিফাত পরে জড়ো হওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে এই স্লোগান তোলে।
১৪ই জুলাই রাত ১১টা ৩৪ মিনিটে ‘তুমি কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার-স্বৈরাচার’ এই স্লোগান তোলার মধ্য দিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি থেকে হাসিনাকে গোটা বাংলাদেশে ‘স্বৈরাচার’ শব্দে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এটি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি বড় অর্জন, যা অনেক সাংবাদিকও স্বীকৃতি দিয়েছেন।
বাসস: আমরা দেখেছি ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ বিতাড়িতসহ নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এই দিনগুলোতে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
আবিদুল ইসলাম খান: ১৫ই জুলাই সকাল ১১টায় রাজু ভাস্কর্যে শিক্ষার্থীদের একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। হলগুলোতে যখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের মিছিলে অংশ নিতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল, তখন শিক্ষার্থীরা সেই বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। এতে হল পাড়ায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ করে। এই সময়ে আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম এবং এই হামলায় আহত হয়ে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।
এদিন দুপুর ১২ টার দিকে রাজু ভাস্কর্যে পৌঁছে দেখি রাজু ভাস্কর্যে কেউ নেই, সবাই সূর্যসেন হলের সামনে মাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিজয় ৭১ এ সংঘর্ষ চলছে। সংঘর্ষ শুরুর সময় আমরা সবাই মিলে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলি। অসংখ্য মেয়েরাও সেদিন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। পরে যখন আমরা ভিসি চত্বরে আসি, তখন বৃষ্টির মতো ইট নিক্ষেপ করা শুরু হয়। বড় বড় ইটের আঘাতে অনেকের মাথা, কপাল, শরীর এবং হাত-পা থেঁতলে গিয়েছিল। আমি মেয়েদের ভিড়ের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলাম। এর মাঝেই ছাত্রলীগের রডের আঘাত আমার পায়ে লাগে এবং আমি পড়ে যাই। কোনোমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসএম হলের ভেতরে ঢুকি। তখন বিজয় ৭১ হলের দপ্তর সম্পাদক সাকিব বিশ্বাস এবং কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদলের মানবাধিকার সম্পাদক শাহাদাত আমাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
সেদিনের নির্মমতা এবং মেয়েদের ভূমিকা ছিল অভাবনীয়। মেয়েদের এভাবে সংগ্রামে নামাটা আন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি ডাক্তাররা কে কার চিকিৎসা দেবেন, তা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের কিছু নেতার নেতৃত্বে আমার এক্স-রে করানো হয়। পা ভাঙেনি, কিন্তু মারাত্মক ব্যথা ছিল। যেহেতু ভাঙেনি, তাই আমাকে ইসলামিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এরপর জানতে পারি, ছাত্রলীগ ঢাকা মেডিকেলের ভেতরেও হামলা চালিয়েছে এবং রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের ওপরও আক্রমণ করেছে।
ডাক্তার আমাকে পরামর্শ দেন প্লাস্টার করার। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করি, কারণ প্লাস্টার করলে আন্দোলন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম।
১৫ জুলাই আমাদের ওপর হামলার পর বিকেলে জরুরি ভিত্তিতে বিএনপি পার্টি অফিসে একটি মিটিং ডাকা হয়। ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয় সেদিন রাত থেকেই সশরীরে আন্দোলনে নামার জন্য। ১৫ই জুলাই বিকেলে শহীদুল্লাহ হলের সংঘর্ষে ছাত্রদল পুরোপুরি সাংগঠনিকভাবে উপস্থিত ছিল।
১৬ই জুলাই শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি ছিল। আমার পায়ের অবস্থা তখনো ভয়াবহ, দাঁড়াতেও পারছিলাম না। কিন্তু মন মানছিল না। বাসায় থাকতে পারছিলাম না। তাই আমি সিফাত ইবনে আমিন ও আরও দু'জনকে আমার খিলক্ষেতের বাসায় ডাকি। তারা সিএনজি করে আমাকে শহীদ মিনারের দিকে নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা যখন আসি, তখন শহীদ মিনারে ঢোকার কোনো উপায় ছিল না। বকশিবাজার ও ঢাকা মেডিকেলের গেট দিয়ে ঢোকার অনেক চেষ্টা করেও পারিনি।
১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক। নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থী বাদে যারা সেদিন ক্যাম্পাসে ছিল তাদের বেশিরভাগ ছাত্রদলের নেতাকর্মী। ১৭ জুলাই সকাল ১১টায় সারাদেশে ১৬ জুলাই শহীদ হওয়া ৬ জনের গায়েবানা জানাজা ছিল। সেদিন আমি ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলাম না। কারণ ১৫ জুলাইয়ের আঘাতের কারণে আমার পা তখনো ভয়াবহ অবস্থায় ছিল। শারীরিক শক্তি নয়, মানসিক শক্তি দিয়ে আমি চলাফেরা করছিলাম। গায়েবানা জানাজার জন্য যে কফিন আনা হয়েছিল, তার সামনে ছাত্রদলের ফ্রন্টলাইনাররা, যেমন সাইফ, হামিম এবং অন্যরা উপস্থিত ছিল।
বাসস: ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এর পরে কীভাবে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন?
আবিদুল ইসলাম খান: ১৮ জুলাই আন্দোলনকে সচল রাখাটা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছাড়া হয়েছিল। এদিন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলনকে সজীব করে তোলে। ১৮ই জুলাই সকালে আমি যখন বসুন্ধরা গেটে যাই, সেখানে মাইক হাতে নিয়ে যখন আমি গম্ভীর কণ্ঠে স্লোগান শুরু করি, পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। রাস্তার দুই পাশ থেকে মানুষের ঢল নামে। আমাদের সাথে যোগ দেয় সবাই। নর্থ সাউথ, আইইউবি, এআইইউবি-সহ সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেদিন এক বিপ্লব ঘটায়।
ভাটারা থেকে যখন আমাদের ওপর হামলা হয়, তখন রক্তাক্ত অবস্থায় টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত একটি ছেলেকে নিয়ে আমরা বাড্ডার একটি বাড়িতে ঢুকি। সেই বাড়ির সব আন্টিরা এসে ফ্যান, খাবার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে আহত ছেলেটির সেবা করা শুরু করেন। তারা আমাকে ওয়াইফাই কানেকশন দেন এবং বলেন বাইরে আপডেট দিতে। তখন মোবাইল নেটওয়ার্ক বা কোনো সাংবাদিকও ছিল না। আমি একটি ভিডিও বার্তা দিই, ‘কে কোথায় আছেন, নেমে পড়ুন! বাড্ডায় রক্তাক্ত পরিস্থিতি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র রাজপথ ছেড়ে যাচ্ছে না।’ সেই বাসার এক আন্টি আমাকে তিনটি মোটা লাঠি এবং টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য একটি পেপসোডেন্ট টিউব ও দিয়াশলাই দিয়েছিলেন।
এরপর ১৮ই জুলাই রাত থেকে টোটালি নেট বন্ধ হয়ে যায়। ওই রাতে যখন আমি বাসা থেকে বের হই, তখন দেখতে পাই পুরো রাস্তা মানুষে ভরা। মুরুব্বীরাও রাস্তায় নেমেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার ওই এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়, এতে অসংখ্য মানুষ আহত হয়।
রাত ৮-৯টার দিকে আমি যখন রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করি, তখন প্রতিটি মোড়ে মোড়ে আমাকে চেক করা হচ্ছিল যে আমি ছাত্রলীগ কি না। এটা দেখে আমার মনে অনেক শান্তি লেগেছিল যে, এত দিন যারা আমাদের ফোন চেক করত, আজ তাদের ফোন চেক করা হচ্ছে। প্রতিটি মোড়ে পাহারাদার ছিল।
১৯ জুলাই শুক্রবার ছিল। আমাদের কাছে ফোন আসে যে বিএনপির একটি সমাবেশ আছে। এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় আসার মতো অবস্থা ছিল না। বসুন্ধরা এলাকায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ থাকায় আমি শুক্রবার সকালে বসুন্ধরা গেটের কাছে একটি পরিচিত কাজী অফিসে গিয়ে বসি। সেখান থেকে আমি সবাইকে ফোন দিচ্ছিলাম। অনেকে বলছিল, ‘ভাই, আসব।’ আমি দেখতে পেলাম যে আইয়ুব নামের একটি ছেলে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে গিয়ে মাইকিং করছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা থাকে এবং বলছে ‘নেমে আসুন, নেমে পড়ুন।’
পরে বসুন্ধরা গেটে দাঁড়িয়ে দেখলাম অন্তত ১০ হাজার মানুষের একটি মিছিল। সেখানেই আমরা মোটামুটি অবরোধ করি, রাস্তা এবং কারফিউ ভাঙি। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়াই, স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাথেও সংঘর্ষ হয়। ঠিক ৪টা থেকে ৫টার দিকে আবার হেলিকপ্টার থেকে হামলা করা হয়। চোখের সামনে অসংখ্য মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেদিন এতো মানুষের মিছিল দেখে আমার মনে হয়েছিল, রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসা কাকে বলে! একদিকে পরিবার, অন্যদিকে রাষ্ট্র—তারা সেদিন রাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছিল। ওইদিন অসংখ্য ছেলেমেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
সেদিন রাতেই আমরা ঘোষণা দিই যে পরদিন সকাল ৯টায় আবার একত্রিত হব। ২০শে জুলাই সকালে যখন সেখানে গেলাম, তখন দেখলাম প্রচুর মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পরে সেদিন আমরা সেখানে আন্দোলন গড়ে তুলি। এভাবে নেট বন্ধের দিনগুলোতে আমি এই এলাকায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম। এই সময় অনেক লোক মারা গিয়েছিল এবং অনেকেই আহত হয়েছিল।
তিন-চার দিন পর সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রেস ক্লাবে একটি মিছিল করে, যা ছিল এই আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি নতুন পন্থা। এরপর ‘মার্চ ফর জাস্টিস’-এ আইনজীবীরা নেমে আসেন, সাংস্কৃতিক কর্মীরা ফার্মগেট থেকে শুরু করে সব জায়গায় মিছিল করেন, বুদ্ধিজীবীরা মাঠে নেমে আসেন। ১৯শে জুলাই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত সময়টা ছিল চূড়ান্ত গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার সৃষ্টির সময়। রেমিটেন্স যোদ্ধা, শিক্ষক, আইনজীবী, শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর, এমনকি রাস্তার পথশিশুদের ভূমিকাও এই গণঅভ্যুত্থানে অসাধারণ ছিল। যখন সবাই নেমে আসে, তখন আন্দোলন ধীরে ধীরে এক দফার দিকে চূড়ান্তভাবে এগিয়ে যায়।
বাসস: ২ আগস্ট থেকে ৪ আগস্ট আপনার অভিজ্ঞতা বলুন?
আবিদুল ইসলাম খান: আগস্টের ২ তারিখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আন্দোলন এক দফার দিকে যাচ্ছে এবং চূড়ান্ত ঘোষণা আসার পথে। ৩ আগস্ট সকাল থেকেই সেই প্রস্তুতির প্রতিফলন দেখা যায়। ওইদিন দুপুর ১২টার দিকে আমি সবার আগে শহীদ মিনারে আসি। এসে দেখি আমাদের শহীদুল্লাহ হল ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নূর এক দফার স্লোগান দিয়ে কিছু মানুষকে জড়ো করে রেখেছেন। সকালে অনেকের ভয় ছিল, আমরা এসে সেই ভয় কাটাই। পুরো শহীদ মিনার পদত্যাগ, পদত্যাগ, পদত্যাগ স্লোগানে প্রকম্পিত হতে শুরু করে, ঘোষণা আসার আগেই।
এরপর এক দফার ঘোষণা আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রো রেলের পিলার থেকে হাসিনার ছবিকে সর্বপ্রথম ছাত্রদলের সবাই মিলে মুছে দেয়। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগের নিদর্শনগুলোর ওপর ছাত্রদল ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।
৪ তারিখ সবার সাথে সমন্বয় করে সকাল ৯টায় শাহবাগে আসি। এদিন শাহবাগে যুবলীগের সাথে বিশাল সংঘর্ষ হয়। আমরা তাদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দিই। পিজি হাসপাতালে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানকার ছাদ থেকে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়। সবকিছু মিলিয়ে আমরা তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শাহবাগ দখল করি। সেদিন সারাদিনে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। এদিন সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত আমি শাহবাগে অবস্থান করি।
বাসস: ৩৬ জুলাইয়ে কীভাবে বিজয় উদযাপন করেছিলেন?
আবিদুল ইসলাম খান: ৪ জুলাই রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিই। সেই সময়ে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ সামনে ছিল না। সারারাত কেঁদে জীবনের সকল ভুলের জন্য ক্ষমা চাই। তাহাজ্জুদ পড়ে ঘুমালাম। সারা রাত আমার শরীরে বৃষ্টি পড়ার অনুভব হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সাহস সঞ্চারিত হচ্ছে। সকালে আমি কোনো ভয় ছাড়াই আনন্দের সাথে ঘুম থেকে উঠি এবং বাসা থেকে বের হই।
শহীদ মিনারের দিকে যখন যাচ্ছিলাম, তখন গুলির শব্দ শুনি। জানতে পারি সবাই মেডিকেলে এসেছে। আমি শহীদ মিনারে না গিয়ে মেডিকেলে ঢুকি। ঢাকা মেডিকেলের নতুন বিল্ডিংয়ে পরিচিত কয়েকজনের সাথে কথা বলি, জানতে চাই, ‘এখন কী করা যায়?’ তারা বলে, ‘ভাই, আমাদের তো নামতে হবে।’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, নামতে হবে।’ সেখানে ছাত্রদলের অনেককে খুঁজে পাই। পরে আমি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলি, ‘এখানে যারা আমার মা-বাবা, ভাই-বোন আছেন, এই যুদ্ধের ময়দানে আমাদের পাশে থাকুন। আমরা এ লড়াইয়ে জিতব, কোনো সন্দেহ নেই। আজকেই জিতব! প্লিজ কেউ কাউকে ছেড়ে যাইয়েন না।’ এই ‘আজকেই জিতব’ কথাটা কীভাবে আমার মুখ থেকে এসেছিল, আমি নিজেও জানি না।
আমি যখন সবাইকে হাত উঁচু করে প্রতিজ্ঞা করালাম, ‘আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না।’ তখন এক হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
এরপর সবাই মিলে, একত্রিত হয়ে, আমরা হাতে কোনো অস্ত্র বা সুরক্ষা ছাড়াই শুধু শরীর আর সাহস নিয়ে মাঠে নেমে পড়ি। এরপর পুলিশের গুলিতে ইনস্ট্যান্ট দুজন শহীদ হন। যে ছেলেটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনার সময় সবচেয়ে উজ্জীবিত ছিল, সেই মানিক মিয়া পুলিশের গুলিতে সর্বপ্রথম আমার সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে মারা না গেলে হয়ত আমি মারা যেতাম। এরপর আমার সামনে আনাসও শহীদ হয়। আনাস শহীদ হওয়ার পর আমাদের ওপর হামলা কিছুটা কমে। তবে ওই সময় আরও তিনজন শহীদ হয়। পাঁচজন শহীদ হওয়ার পর প্রায় ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাই।
পরে পুলিশের সাথে আমরা টিকতে না পেরে আবারও ঢাকা মেডিকেলে ঢুকি। সেখানে অপজিট বিল্ডিং থেকে স্নাইপারের মাধ্যমে আমাদের ওপর আক্রমণ করছিল যুবলীগের সন্ত্রাসীরা।
পরে সাড়ে ১১ টার দিকে আমি পলাশী মোড়ের দিকে যাই। পলাশীতে যখন আসছিলাম, তখন একদল সেনাবাহিনী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের কাছে জোর গলায় বলতে থাকি, ‘আপনারা কী করছেন? আমাদেরকে মেরে ফেলছে, আমাদের পাশে দাঁড়ান।’ সেই সেনাবাহিনী হাত উঁচিয়ে আমাকে মুষ্টি দেখিয়েছিল, তখন আমি সাহস পেয়েছিলাম। এরপর আমি পলাশীতে আসি। এসে অনেক শিক্ষার্থী এবং পরিচিত ছাত্রদল কর্মী দেখে তাদের নিয়ে ফ্রন্টলাইনে মিছিল করে শাহবাগের দিকে অগ্রসর হই। শাহবাগের কারফিউ ভেঙে শাহবাগ চত্বর দখল করি। তখন আমি স্লোগান দিয়েছিলাম, ‘এই মুহূর্তে খবর হলো, খুনি হাসিনা পালিয়ে গেল।’ এর ঠিক আধা ঘণ্টা পর হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যান।
আমার একটি স্বপ্ন ছিল, হাসিনা যেদিন চলে যাবে, সেদিন আমি রাজপথে ঘুমাবো। হাসিনার পতনের পর উল্লাস করে আমি আধা ঘণ্টা থেকে ৪০ মিনিট ঘুমিয়েছি...।
বাসস: গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে আপনার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন কি?
আবিদুল ইসলাম খান: ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর বিএনপি ক্ষমতায় আসবে এই স্বপ্নে আমি ছাত্রদলে যোগ দেইনি। আমি ছাত্রদলকে খুঁজে বের করেছি রাষ্ট্রের স্বার্থে, একটি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলই ছিল আমার বেছে নেওয়া সংগঠন। আমার ডিপার্টমেন্টের বন্ধুরা, ইয়ারমেটরা, ব্যাচমেটরা পর্যন্ত আমার সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেনি, কারণ আমার সাথে ছবি তুললে তাদের সরকারি চাকরি হবে না, হলে থাকতে পারবে না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আমরা রাজনীতিতে টিকে ছিলাম।
আমার চাওয়া হচ্ছে এই বাংলাদেশে আর কখনো প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত না হোক। প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে, সকল মত-পথ, হিংসা সবকিছুকে ছাড়িয়ে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আদর্শের নীতিতে একটি বৈষম্যহীন, সম্প্রীতিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠন করাটাই হবে এখন আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।